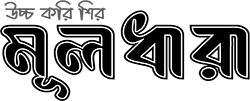বাংলাদেশের রাজনীতি যেন বরাবরই এক অদৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্রের মতো। এখানে যোগ্য ও নীতিবান নেতারা তাদের সামর্থ্য বা আদর্শ দিয়ে মানুষের আস্থা অর্জনের আগেই অনেক সময় পরিণত হন লক্ষ্যবস্তুতে। মিথ্যা কুৎসা, অপপ্রচার, সম্পাদিত ছবি-ভিডিও এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের মাধ্যমে তাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হয়। দুঃখজনকভাবে বর্তমানে এটি কমন ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে।
বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বৈশ্বিক রাজনীতিতে character assassination একধরনের বৈধ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এর মূল উদ্দেশ্য কেবল একজন ব্যক্তিকে আঘাত করা নয়, বরং জনপরিসরে এমন এক ভীতিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা, যাতে সম্ভাব্য নেতৃত্ব নিজে থেকেই পিছিয়ে যায়। ক্রিস্টোফার পল ও মিরিয়াম ম্যাথিউস তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন— তথ্যযুদ্ধ (information warfare) এখন আর রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ নয়; এটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরেও প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার কার্যকর কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
গণতন্ত্র তখনই টিকে থাকে, যখন জনপরিসরে মুক্ত বিতর্ক ও সত্যভিত্তিক যুক্তি বিনিময় সম্ভব হয়; কিন্তু যখন এই পরিসর ভুয়া খবর ও চরিত্রহননের মাধ্যমে দূষিত হয়, তখন জনমত আর যুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হয় না। বরং ভয়, সন্দেহ ও আবেগ দ্বারা পরিচালিত প্রতিক্রিয়া প্রধান হয়ে যায়। এভাবে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি দুর্বল হয় এবং রাজনীতি চিন্তার প্রতিযোগিতার বদলে প্রতিপক্ষকে অবমূল্যায়ন ও ধ্বংস করার খেলায় পরিণত হয়।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই কৌশল, বিশেষ করে বিগত ১৬ বছরের ক্ষমতাকেন্দ্রিক শাসনে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছিল। সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী, ছাত্রনেতা— কেউই এ থেকে রেহাই পাননি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন এবং প্রভাবশালী অনলাইন নিউজ পোর্টাল— সব ক্ষেত্রেই কখনো গোপনে, কখনো প্রকাশ্যে এই প্রচারণা চালানো হয়েছে। ৫ আগস্টের পর অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পরও চরিত্রহননের কৌশল থামানো যায়নি; বরং তা যেন আরো সুসংগঠিত ও পরিপক্ব রূপ ধারণ করেছে। ভিত্তিহীন আর্থিক কেলেঙ্কারি, যাচাইহীন ‘চাঁদাবাজির অভিযোগ’ কিংবা সম্পাদিত ভিডিও— সবই চরিত্রহননে ব্যবহৃত হচ্ছে ধারালো তলোয়ার হিসেবে। অবশ্য কিছু সুবিধাভোগী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত, যা অস্বীকার করার উপায় নেই।

AI-এর যুগে অপপ্রচারের কৌশল আরো সূক্ষ্ম ও ছলনাময় হয়ে উঠেছে। অচেনা পেজ বা ভুয়া আইডি থেকে হঠাৎ করে গুজব ছড়ানো হয়। AI-ভিত্তিক ছবি বা ভিডিও সম্পাদনার মাধ্যমে পুরোনো ঘটনা নতুন ঘটনার মতো উপস্থাপন করা হয়। ফলে বিভ্রান্তিকর থাম্বনেইল ও অসংগতিপূর্ণ ক্যাপশন সাধারণ পাঠকের মনকে করে তোলে সন্দিহীন। প্রকৃত সত্যের বদলে জনমনে সন্দেহ স্থায়ী হয়ে যায়।
এই পরিস্থিতি বোঝার জন্য জার্গেন হাবারমাসের public sphere ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ। এর সারকথা হলো, গণতন্ত্র তখনই টিকে থাকে, যখন জনপরিসরে মুক্ত বিতর্ক ও সত্যভিত্তিক যুক্তি বিনিময় সম্ভব হয়; কিন্তু যখন এই পরিসর ভুয়া খবর ও চরিত্রহননের মাধ্যমে দূষিত হয়, তখন জনমত আর যুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হয় না। বরং ভয়, সন্দেহ ও আবেগ দ্বারা পরিচালিত প্রতিক্রিয়া প্রধান হয়ে যায়। এভাবে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি দুর্বল হয় এবং রাজনীতি চিন্তার প্রতিযোগিতার বদলে প্রতিপক্ষকে অবমূল্যায়ন ও ধ্বংস করার খেলায় পরিণত হয়।
হেরমান ও চমস্কির propaganda model এ প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তারা দেখিয়েছেন, গণমাধ্যম প্রায়শই ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে, যেখানে বিজ্ঞাপন, মালিকানা ও রাজনৈতিক প্রভাব সংবাদ নির্বাচনে প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের বাস্তবতাও সেই কথা বলে!
সন্দেহ নেই, চরিত্রহননের রাজনীতি এখন বৈশ্বিক বাস্তবতা। লাতিন আমেরিকা, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পাকিস্তান— সবখানেই বিরোধী নেতা, শিক্ষাবিদ বা মানবাধিকারকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশে এর প্রভাব সীমিত বটে। তবে যেসব দেশে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারেনি, সেখানে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে। দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশ এই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
এ ধরনের অপপ্রচার শুধু একক ব্যক্তিকে নয়, বরং ক্ষতিগ্রস্ত করে গোটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে। যোগ্য নাগরিকরা রাজনীতিতে প্রবেশ করতে হিমশিম খান। এর কারণ, তারা জানেন— রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন কিংবা কাজের মূল্যায়ন বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হতে পারে। নীতি বা দক্ষতার চেয়ে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার চিন্তাই প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। এই সংস্কৃতি সত্যিই ভীতিকর।
চরিত্রহননের রাজনীতির এই চক্র ভাঙতে হলে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনা জরুরি। নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা কুৎসা বা অপপ্রচারের মাধ্যমে নয়; বরং নীতি, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে হতে হবে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাখা, রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র নিশ্চিত করা এবং গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শক্তিশালী তথ্য যাচাই ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। সর্বোপরি প্রয়োজন নাগরিক সচেতনতা।
লেখক : বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।
(এই লেখা লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত; এ সংক্রান্ত কোনো দায় দৈনিক মূলধারা বহন করবে না)