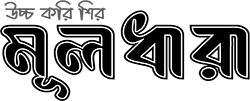একসময় গণমাধ্যম বলতে বোঝাত রেডিও, টেলিভিশন কিংবা পত্রিকাকে। কিন্তু প্রযুক্তির অগ্রগতির ঢেউ এনে দিয়েছে এক নতুন যুগ, যেখানে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন টিকটক বিশ্বব্যাপী এক বিপুল প্রভাব ফেলেছে। ২০১৬ সালে চীনে Douyin নামে যাত্রা শুরু করে, ২০১৮ সালে এটি TikTok নামে বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ৩ বিলিয়নেরও বেশি ডাউনলোড হয়েছে, যার বড় অংশই ১৬ থেকে ২৫ বছর বয়সি তরুণ।
টিকটক একটি গণমাধ্যম, যেখানে যে কেউ একটি মোবাইল ক্যামেরা দিয়েই হয়ে উঠতে পারে ‘স্টার’। অনেক তরুণ-তরুণী অভিনয়, নাচ, কবিতা, সংলাপ কিংবা নিজের ভাবনা দিয়ে ভিডিও তৈরি করছেন। কেউ কেউ নাটক, বিজ্ঞাপন বা সিনেমাতেও সুযোগ পেয়েছেন এই মাধ্যম থেকেই।
এই অ্যাপটি কেবল বিনোদনের জন্য নয়—অনেকে এখানে নারীর অধিকার, আত্মহত্যা প্রতিরোধ, পরিবেশ সচেতনতা বা মাদকবিরোধী বার্তাও ছড়িয়ে দিচ্ছেন সৃজনশীলভাবে। কোভিড-১৯ মহামারির সময়, টিকটকের মাধ্যমেই অনেকে স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে সচেতনতামূলক ভিডিও বানিয়েছেন।
শিক্ষাক্ষেত্রেও এর সম্ভাবনা রয়েছে। কেউ গণিত বা ইতিহাসকে মজার গল্পে উপস্থাপন করছেন, কেউ ইংরেজি শেখার সহজ টিপস দিচ্ছেন। তরুণদের শেখার আগ্রহ বাড়াতে এটি কাজও করছে।
তবে প্রশ্ন হচ্ছে—এই সৃষ্টিশীলতা কতটা গভীর? অনেকেই ‘ভাইরাল’ হওয়া এবং ‘ভিউ’ পাওয়ার নেশায় ভিডিও তৈরি করছেন। আপত্তিকর পোশাক, অশালীন অঙ্গভঙ্গি, ব্যক্তিগত বিষয়কে উদ্ভটভাবে উপস্থাপন করে ‘লাইক’ আদায় করাই যেন প্রধান লক্ষ্য। এতে নতুনত্ব হারিয়ে কনটেন্ট হয়ে যাচ্ছে একঘেয়ে এবং কপি-পেস্ট।
সবচেয়ে বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে কিশোর-কিশোরীরা। সাজানো ‘ফেক লাইফস্টাইল’ দেখে তারা নিজেদের বাস্তবতা তুচ্ছ মনে করে, হতাশায় ডুবে যায়। গবেষণায় বলা হচ্ছে, এই লাইক পাওয়ার প্রতিযোগিতা একধরনের ডোপামিন রাশ তৈরি করে, যা মস্তিষ্কে অস্থায়ী আনন্দ এনে দেয় এবং এক ধরনের আসক্তি তৈরি করে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক জরিপে দেখা গেছে, তরুণদের মধ্যে মানসিক অস্থিরতা, আত্মসম্মানহীনতা ও বিষণ্নতার পেছনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনপ্রিয় হওয়ার চাপ একটি বড় কারণ।
তবে টিকটক একপাক্ষিক নয়। অনেকেই এর মাধ্যমে স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি, লোকগান, গল্প, রসিকতা বা কবিতা তুলে ধরছেন। বিশেষ করে, প্রান্তিক অঞ্চল থেকে উঠে আসা কণ্ঠগুলো নতুন পরিচয় পাচ্ছে। অনেকেই সাহিত্য ও নাট্যরূপে কনটেন্ট তৈরি করছেন, যা রুচিশীলতাও বজায় রাখছে।
কিন্তু এর বিপরীতে রয়েছে ট্রেন্ডধর্মী, অশালীন বা একঘেয়ে কনটেন্ট—যা ভাষা ও আচরণের অবনতি ঘটাচ্ছে। শিশুরাও এসব দেখে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতের জন্য অশনিসংকেত।
তাই প্রশ্ন উঠছে—দায় কার? শুধু কি ব্যবহারকারীর? নাকি পরিবার, শিক্ষাব্যবস্থা ও রাষ্ট্রও এর জন্য দায়ী?
শিক্ষকরা যদি ডিজিটাল লিটারেসি শিক্ষা দেন এবং শেখান যে সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তা জীবনের সাফল্য নয়, তবে শিক্ষার্থীরা সঠিক পথে এগোতে পারে। অভিভাবকদেরও সন্তানের কনটেন্ট ও আচরণের প্রতি সচেতন নজর রাখতে হবে।
রাষ্ট্রকেও নীতিগত ভূমিকা রাখতে হবে। অশালীন কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা, শিক্ষা পাঠ্যক্রমে ডিজিটাল আচরণ অন্তর্ভুক্ত করা এবং ভালো কনটেন্ট নির্মাতাদের স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।
এছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম চালু করে কনটেন্ট নির্মাতাদের নৈতিক ও সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরিতে উত্সাহ দেওয়া যেতে পারে। পরিবেশ, স্বাস্থ্য, নারী অধিকার কিংবা শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও তৈরিতে পুরস্কার ঘোষণাও হতে পারে কার্যকর।
এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আমরা বলতেই পারি, টিকটক আমাদের সামনে একটি দ্বৈত দিক উন্মোচন করেছে—একদিকে এটি সম্ভাবনার দুয়ার খুলেছে, অন্যদিকে সৃষ্টি করেছে বিভ্রান্তি ও সস্তা জনপ্রিয়তার ফাঁদ।
তরুণদের প্রতি বার্তা স্পষ্ট—প্রযুক্তি ব্যবহার করো, তবে দায়িত্ব নিয়ে। ভাইরাল হওয়া নয়, নৈতিকতা ও চিন্তার গভীরতাই তোমার আসল পরিচয়। সৃজনশীলতা দীর্ঘস্থায়ী, জনপ্রিয়তা নয়।
সোশ্যাল মিডিয়া যেন আমাদের নিয়ন্ত্রণ না করে—বরং আমরা নিজ বিবেক দিয়ে সিদ্ধান্ত নিই। প্রশ্ন রেখে যাই—টিকটক কি আজ সত্যিই আমাদের কণ্ঠস্বর, নাকি নিছক এক শোরগোল?