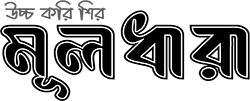ইতিহাসের পাতায় রক্ত, আগুন ও ধ্বংসস্তূপের যেসব করুণ কাহিনি ছড়িয়ে আছে, তার কেন্দ্রে যুদ্ধ। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ঠান্ডা যুদ্ধ, আফগান-ইরাক সংঘাত, সিরিয়া-সংকট, ইসরাইল-প্যালেস্টাইন বিরোধ, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বা সাম্প্রতিক ইরান-ইসরাইল উত্তেজনা—এসব কেবল রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বা কূটনৈতিক ব্যর্থতা নয়; বাস্তবতা আরো গভীর ও পুঁজিকেন্দ্রিক। অস্ত্র ব্যবসা, ধ্বংসস্তূপে নির্মাণ খাত, দখলকৃত ভূখণ্ডে প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ, নিরাপত্তা প্রযুক্তির রপ্তানি এবং শরণার্থী ব্যবস্থাপনায় দাতা সংস্থার বাজেট বৃদ্ধি—সব মিলিয়ে যুদ্ধ এখন এক সুসংগঠিত অর্থনৈতিক কাঠামো।
জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বৈশ্বিক সামরিক ব্যয় ছিল ২.৪ ট্রিলিয়ন ডলার, যা মানব উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের তুলনায় বহু গুণ বেশি। যুদ্ধের নামে এই পরিকল্পিত ব্যবসা মানবিক মূল্যবোধ ও আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে; শান্তিকে নয়, বরং অশান্তিকে পুঁজি করে টিকে থাকে।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) ছিল আধুনিক ইতিহাসের প্রথম ‘শিল্পায়িত যুদ্ধ’। যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরেও তৈরি হয় ‘রণ-শিল্প’ নামের এক অদৃশ্য ফ্রন্ট। ইউরোপ ও আমেরিকায় অস্ত্র ও সরঞ্জামের চাহিদা নাটকীয়ভাবে বাড়ে। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের শুরুতে নিরপেক্ষ থেকেও বিপুল অস্ত্র, খাদ্য ও চিকিত্সাসামগ্রী রপ্তানি করে অর্থনৈতিক মুনাফা তোলে। রথচাইল্ডদের মতো ব্যাংকিং পরিবার যুদ্ধরত দেশগুলোর ঋণদাতা হয়ে ওঠে। বিমা কোম্পানিগুলোও যুদ্ধে ব্যবহূত সরবরাহ ব্যবস্থার বিমা দিয়ে লাভবান হয়। প্রায় ১ কোটি প্রাণহানির এই যুদ্ধে অস্ত্র ব্যবসায়ীরা বিপুল মুনাফা করে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ, তবে এটি শুধুই ধ্বংস নয়, বরং এক সুবিশাল শিল্পও। যুদ্ধের আগেই যুক্তরাষ্ট্র বিপুল অস্ত্র রপ্তানি করে লাভবান হচ্ছিল। জেনারেল মোটরস, বোয়িং, লকহিডসহ অসংখ্য কোম্পানি যুদ্ধবিমান, ট্যাংক, রাডার তৈরি করে বিলিয়ন ডলার আয় করে। যুদ্ধ-উত্তর ইউরোপ পুনর্গঠনের নামে মার্কিন ‘মার্শাল প্ল্যান’ নতুন বাজার তৈরি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রমাণ করে, যুদ্ধ রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক হিসাবেরও খেলা। এতে অস্ত্র প্রস্তুতকারক, নির্মাণ ও প্রযুক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো এক ধরনের করপোরেট চক্রে পরিণত হয়, যার মূল প্রতিপাদ্য—‘মৃত্যুর বিনিময়ে মুনাফা’।
ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৫-১৯৭৫) ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ব্যয়বহুল যুদ্ধ—বর্তমান দামে যার খরচ ৭৩৫ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এই ব্যয়েও করপোরেট গোষ্ঠীগুলোর মুনাফা হয় বিপুল। লকহিড ও বোয়িংয়ের মতো অস্ত্র কোম্পানি হাজার হাজার যুদ্ধবিমান সরবরাহ করে। বেসরকারি ঠিকাদাররা সৈন্য পরিবহন ও খাদ্য সরবরাহের নামে কোটি কোটি ডলার আয় করে।
আফগানিস্তান যুদ্ধ (২০০১-২০২১) ছিল আমেরিকার দীর্ঘতম যুদ্ধ, যার ব্যয় ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। সামরিক ঠিকাদার কোম্পানিগুলো ঘাঁটি নির্মাণ, নিরাপত্তা এবং সরঞ্জাম সরবরাহের নামে শত শত বিলিয়ন ডলারের চুক্তি পায়। অস্ত্র নির্মাতারা প্রতিনিয়ত ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করে এবং মার্কিন কংগ্রেসে লবিস্টদের মাধ্যমে বাজেট বাড়ায়।
ইরাক যুদ্ধ (২০০৩-২০১১) এর সময় হালিবার্টন একাই প্রায় ৩৯ বিলিয়ন ডলারের সরকারি চুক্তি পায়। ইরাকের তেল খাতে এক্সনমোবিল, বিপি, শেলের মতো বহুজাতিক কোম্পানির প্রবেশাধিকারে যুদ্ধের আর্থিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। প্রাইভেট মিলিটারি কোম্পানিগুলো অনেক সময় আইনের ঊর্ধ্বে থেকে কাজ করে।
লিবিয়ায় ২০১১ সালে গাদ্দাফিকে সরানোর পর পশ্চিমা তেল কোম্পানিগুলো লিবিয়ার তেলক্ষেত্র দখলে নেয়। সিরিয়া ও ইয়েমেনেও তেল ও প্রাকৃতিক সম্পদকে ঘিরে সামরিক বাণিজ্য পরিচালিত হয়েছে।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ (২০২২-) পশ্চিমা অস্ত্র রপ্তানির নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে ১০৬ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দেয়, যার সিংহভাগই ফিরে আসে মার্কিন শিল্পে। রাশিয়ার গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হলে আমেরিকা ইউরোপে এলএনজি রপ্তানি করে বিপুল মুনাফা তোলে। ২০২৫ সালের এক চুক্তি অনুযায়ী, ইউক্রেনি সম্পদের রাজস্বের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ভবিষ্যতে মার্কিন অংশীদারিত্বের সুযোগ তৈরি হয়েছে।
২০২৪-২৫ সালের ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘর্ষেও ড্রোন, আয়রন ডোম, নজরদারি প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার ঘটে। এসব পণ্যের রপ্তানি ইসরাইলি প্রতিরক্ষা খাতের আয়ের নতুন পথ খুলে দেয়। উপসাগরীয় দেশগুলো নতুন নিরাপত্তা চুক্তি করে পশ্চিমা অস্ত্র কিনছে, যার সুফল যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর ঘরে।
মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো যুদ্ধনির্ভর অর্থনীতির অন্যতম শিকার। বিশ্বে প্রমাণিত তেলের প্রায় ৬০ শতাংশ এই অঞ্চলে। অথচ এরা বছরে শত শত বিলিয়ন ডলার অস্ত্র কিনে পশ্চিমা সামরিক শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখে। তেল যেন আশীর্বাদ নয়, বরং এক অভিশাপ—যার কারণে অঞ্চলের মানবিক ও সামাজিক স্থিতি বিনষ্ট হচ্ছে।
আফ্রিকার কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা, সিয়েরা লিওনের মতো দেশে হিরা ও খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করে গৃহযুদ্ধ চলে, যার পেছনে বহুজাতিক কোম্পানি ও অস্ত্র সরবরাহকারীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত। শীতল যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার যুদ্ধকে আরো ব্যবস্থাপনাভিত্তিক ও লাভজনক বানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন আধুনিক অস্ত্র ও নজরদারি প্রযুক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। ২০২৩ সালে SIPRI-এর তথ্য অনুযায়ী, বৈশ্বিক অস্ত্র বাজারের মূল্য ৫৫০ বিলিয়ন ডলার, যার ৩৯ শতাংশ রপ্তানিই যুক্তরাষ্ট্রের।
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য—যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স—বিশ্বের প্রধান অস্ত্র বিক্রেতা। ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহারে তারা বারবার শান্তিপ্রচেষ্টা ব্যাহত করে। গাজা, সিরিয়া বা ইউক্রেন সংকটে দেখা গেছে, কেবল একটিমাত্র ভেটো কীভাবে মানবিক আবেদনকেও অগ্রাহ্য করে। এই কাঠামোগত পক্ষপাত বিশ্বশান্তিকে এক করপোরেট স্বার্থের কাছে জিম্মি করে রেখেছে।
মানবিকতা, শান্তি ও সামাজিক স্থিতিশীলতা যুদ্ধনির্ভর অর্থনীতির ভেতরে এক প্রহেলিকা মাত্র। সাধারণ মানুষ দুঃখ-কষ্টে জীবন কাটায়, আর করপোরেট জায়ান্টরা গড়ে তোলে অর্থের সাম্রাজ্য। যুদ্ধ তখন বাস্তব শত্রুতার নয়, এক ‘পণ্য’—যা প্যাকেজ করে বিশ্বব্যাপী বিক্রি হয়। তাই যুদ্ধের অর্থনীতিকে চ্যালেঞ্জ করা এবং যুদ্ধপণ্য-নির্ভর শিল্প কাঠামো ভাঙা জরুরি, নচেত্ শান্তি কেবল কাগজেই থাকবে।
বস্তুত, যুদ্ধ কেবল ভূখণ্ডের দখল নয়, এক বিপুল-বিশাল ব্যবসা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে ইসরাইল-ইরান সংঘর্ষ পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধেই অস্ত্র প্রস্তুতকারক, জ্বালানি ব্যবসায়ী ও করপোরেট লবির অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত। প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে যুদ্ধকে আত্মরক্ষামূলক বানিয়ে জনগণকে প্রলুব্ধ করা হয়। পশ্চিমা শক্তিগুলো নিজেরা সরাসরি যুদ্ধে জড়ায় না; বরং প্রক্সি যুদ্ধের মাধ্যমে অস্ত্র বিক্রয় ও অর্থ উদ্ধারে ব্যস্ত। এই প্রক্রিয়া এতটাই জটিল যে, ভুক্তভোগী দেশগুলোর এককভাবে কিছু করার ক্ষমতা নেই—তবে সম্মিলিত প্রতিরোধ ভবিষ্যতে পরিবর্তনের পথ দেখাতে পারে।
লেখক : অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট
(এই লেখা লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত; এ সংক্রান্ত কোনো দায় দৈনিক মূলধারা বহন করবে না)