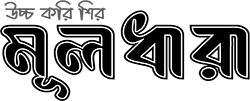দেশ নির্বাচনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু পরিকল্পনা মোতাবেক সম্পাদিত হলে আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দল এবং সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক আলোচনা চলছে। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে আগ্রহ আছে—মানুষ চায় ঠিকমতো ভোট দিয়ে একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসুক। গত ৯ অক্টোবর বিআইডিএসের সভায় অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দীন আহমদও বলেছেন, এ মুহূর্তে সবকিছুর ঊর্ধ্বে দরকার একটি সুষ্ঠু নির্বাচন। কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্যতম শর্ত হলো, প্রার্থীদের মধ্যে যাতে বিশেষ দলের, বিশেষ প্রার্থীদের অর্থশক্তি বা পেশিশক্তি প্রভাব বিস্তার না করে।
অবশ্য ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ স্যার জানেন, আমরাও জানি ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের অধীনে দরিদ্র অর্ধভুক্ত, অশিক্ষিত, অসচেতন ভোটারদের পক্ষে ভয়ভীতি-লোভের ঊর্ধ্বে উঠে ভোট দেওয়াটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এক প্রার্থী জামানতের টাকা বা মনোনয়ন ফি জোগাড় করতে পারলেন না, অন্যদিকে আরেক প্রার্থী কোটি টাকা পকেটে নিয়ে নির্বাচনি ফিল্ডে নামলে নির্বাচনের ফলাফল ভালো হবে না। কালোটাকার মালিকরা অবৈধ অর্থ বিনিয়োগ করে সংসদকে আবারও অসত্ ব্যবসায়ী-আমলা-রাজনীতিবিদদের ক্লাবে পরিণত করবেন।
তার পরেও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে এমন কিছু ন্যূনতম সংস্কার কার্যকর করতে হবে যাতে অর্থের খেলা যথাসম্ভব কমানো যায়। নির্বাচন নিয়ে নানামুখী আলোচনা হলেও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কীভাবে অবৈধ অর্থের প্রভাব মুক্ত করা যাবে তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। অথচ নির্বাচন যদি অর্থের প্রভাবমুক্ত করা না যায়—তাহলে সেই নির্বাচন কখনোই জনপ্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে না। সাংবিধানিকভাবে দিক থেকে বাংলাদেশ হচ্ছে গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অর্থাত্ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের মালিক হচ্ছে সাধারণ জনগণ। সরকার হচ্ছেন জনগণের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমাদের দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক, মজুর তথা নিম্নবিত্ত। আর্থিক সামর্থ্যের দিক থেকে তারা দুর্বল। সাধারণ মানুষ যারা রাষ্ট্রের মালিক তাদেরই তো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের কথা। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিত্তহীন মানুষের পক্ষে নেতা হওয়া বা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করা কঠিন। আমাদের দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াটাই এমন যে, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সাধারণ একজন দরিদ্র মানুষের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কঠিন, তিনি যতই রাজনীতিসচেতন মানুষ হোন না কেন। যোগ্য এবং জনপ্রিয় অনেক ব্যক্তির পক্ষেও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ফলে সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়ে কোনো বিত্তবান ব্যক্তিকে ভোট দিয়ে নির্বাচনে জয়ী করে এবং তাকে নেতা মেনে নেয়। রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই অথচ বিত্তবান এমন ব্যক্তি নেতা হলে আমাদের অর্থনীতি শাস্ত্রের ভাষায় প্রিন্সিপাল-এজেন্ট সমস্যা দেখা দেয়। অর্থাত্ মালিক-প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্কের সমস্যা দেখা দেয়। দেশের মালিক জনগণ, কিন্তু দেশ চালায় মালিকের প্রতিনিধিরা, যাদের আবার নিজস্ব সংকীর্ণ স্বার্থের প্রতিই মনোযোগ বেশি। যেমন, গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমির মালিক জমি চাষ করেন না। জমি চাষ করেন বর্গাচাষিরা। মালিক জমি চাষ করলে উত্পাদন বৃদ্ধির প্রতি যতটা আন্তরিকতা থাকে, বর্গাচাষির মাধ্যমে জমি চাষ করা হলে সেই আন্তরিকতা থাকে না। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যেহেতু রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক দূরে দুর্বল অবস্থানে থাকেন এবং তাদের প্রতিনিধি হিসেবে বিত্তবান শ্রেণির মানুষরাই জবাবদিহিতাবিহীন রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকেন। তাই সেই অবস্থায় জনকল্যাণের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়। বিত্তবান শাসক শ্রেণি সাধারণ মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধারে বেশি তত্পর থাকেন। জনগণ বা সাধারণ ভোটার যারা দেশের মালিক তাদের স্বার্থ একরকম আর যারা নিজেরাই ধনী ব্যবসায়ী বা তাদের থেকে টাকা নিয়ে নির্বাচনি বৈতরণী পারি দিয়েছেন তাদের স্বার্থ অন্যরকম। এখানে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। বিশেষ করে, অসত্ রাজনৈতিক নেতারা যখন অসত্ লোকের কাছ থেকে কালোটাকা নিয়ে বিনিয়োগ করে নির্বাচনে জয়লাভ করে তখন তাদের প্রাথমিক এবং মূল উদ্দেশ্য থাকে নির্বাচনে ব্যয়িত অর্থ সুদে-আসলে তুলে নেওয়া। কিছু মানুষের কাছে নির্বাচন এখন সবচেয়ে লাভজনক বিনিয়োগ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারলে ক্ষমতার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জনের সুযোগ থাকে। কেউ যদি ১০ কোটি টাকা ব্যয় করে নির্বাচন জয়লাভ করে—তাহলে তার প্রচেষ্টা থাকবে কীভাবে মেয়াদকালে অন্তত ১০০ কোটি টাকা আয় করা যায়। এটা একটা নিষ্ঠুর চক্র (Vicious Circle)
নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ করা খুবই কঠিন। কারণ এটা আমাদের মতো পুঁজিবাদী দেশের নির্বাচনি ব্যবস্থায় একটি অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা নির্বাচন ব্যবস্থাকে বৃহত্ ধনিক গোষ্ঠীর বৈধ/অবৈধ অর্থের প্রভাবমুক্ত করতে চাই, তাহলে রাষ্ট্রের যারা মালিক তারা যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে, প্রতিযোগিতায় তাদের জন্যও যাতে উন্মুক্ত স্পেস থাকে—তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রের যারা মালিক তাদের হাতে নির্বাচনে কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই। এটা নির্ধারণ করেন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা। রাজনৈতিক দলের নেতারা এমন ব্যক্তিকেই নির্বাচন মনোনয়ন দান করেন, যারা প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারবেন। দেখা যায়, যারা একসময় অন্য পেশায় ছিলেন, যেমন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, সরকারি চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী এরা নির্বাচনের আগে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রশ্ন হলো, তারা তাদের এতদিনের অভিজ্ঞতা, পেশাগত দক্ষতা পরিত্যাগ করে রাজনীতিতে কেন আসেন? মূলত তারা দুটি কারণে রাজনীতিতে আসতে চান। প্রথমত, রাজনীতিতে যুক্ত হলে রাজনৈতিক পলিসিকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। রাজনৈতিক পলিসিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজবিপ্লব করার কোনো ইচ্ছা তাদের থাকে না, তারা তাদের নিজেদের ও বন্ধুদের ব্যাবসায়িক এবং অন্যান্য স্বার্থ উদ্ধার করতে সচেষ্ট হন। এছাড়া রয়েছে ক্ষমতার মোহ। তারা মনে করেন, আমরা যদি মন্ত্রী অথবা একজন এমপি হতে পারি তাহলেও বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হতে পারব। ক্ষমতা এবং অর্থের মোহ কাটানো খুবই কঠিন। যারা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে নির্বাচনে জয়লাভ করেন, জনগণের সেবা করার মতো উদ্দেশ্য বা মনোভাব তাদের থাকে না বললেই চলে। তবে ব্যতিক্রম নেই তা আমি বলব না। সেরকম সামাজিক ধনী উদ্যোক্তারা সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য উদগ্র হন না। নির্বাচনে টাকার খেলা থেকে মুক্তি পাওয়া বেশ কঠিন হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। আমাদের এমন কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে—যাতে অবসরপ্রাপ্ত আমলা, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা এবং ধনী ব্যবসায়ীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে নিরুত্সাহিত হন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো শীর্ষ নেতৃত্বকে সঠিক পদ্ধতিতে প্রার্থী মনোনয়নের দায়িত্ব নিতে হবে। নির্বাচনে মনোনয়ন দানকালে দলের একনিষ্ঠ কর্মী, যারা দীর্ঘদিন ধরে দলের কর্মকাণ্ডে যুক্ত রয়েছেন, যারা এলাকার ভূমিপুত্র এবং যাদের বিরুদ্ধে নৈতিক স্খলনের কোনো অভিযোগ নেই তাদের মনোনয়ন দিতে হবে, যদি তারা বিত্তবান নাও হন। অর্থাত্ যারা তৃণমূল পর্যায়ে থেকে উঠে এসেছেন, তাদেরই নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে হবে। বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক দলগুলোর একশ্রেণির নেতার বিরুদ্ধে মনোনয়ন বাণিজ্য করার অভিযোগ শোনা যায়। এটা বন্ধ করতে হবে। বিষয়টি নিয়ে আরো কিছু বলার ইচ্ছা রইল।
লেখক : বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অনুলিখন : এম এ খালেক।
(এই লেখা লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত; এ সংক্রান্ত কোনো দায় দৈনিক মূলধারা বহন করবে না)