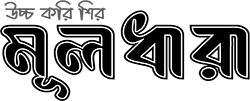বাংলাদেশ এশিয়ার মধ্যে নবম বৃহত্ অর্থনীতির দেশ। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরেই বাংলাদেশের অর্থনীতি সবচেয়ে বড়। ২০২৪ সালের হিসাবের ভিত্তিতে মোট দেশজ উত্পাদনের (জিডিপি) আকার দাঁড়িয়েছে ৪৫০ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য, ৫৪ বছর আগে স্বাধীন হওয়া দেশটি এখনো অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে নাই।
কোনো উন্নয়ন প্রকল্প, মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভর করতে হয়। এমনকি ঘাটতি বাজেট পূরণ করার জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তার প্রয়োজন হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রকল্প গ্রহণ করতে হয়। কারণ, বাংলাদেশে রাজস্ব আয় অনেক কম। কোনো অর্থবছরের শেষে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা কখনো অর্জিত হয় না।
২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। ২০২৫-এর ২৫ জুন পর্যন্ত রাজস্ব সংগ্রহ করা হয় ৩ লাখ ৫৩ হাজার কোটি টাকা। অর্থাত্ রাজস্ব ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা। দুঃখজনক যে, কর-জিডিপি অনুপাতের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন। রাজস্ব আয়ে বাংলাদেশ থেকে নেপাল এবং ভুটান এগিয়ে আছে।
মেগা প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে কঠিন শর্তে ঋণ নিতে হয়। বৈদেশিক ঋণের প্রতিশ্রুতি আসে মূলত দুইভাবে—বাজেট সহায়তা এবং প্রকল্পের ঋণ সহায়তা হিসেবে। বৈদেশিক ঋণের পাশাপাশি সরকারকে দেশীয় উত্স থেকে ঋণ নিয়েও বাজেট ঘাটতি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ব্যয় করতে হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ত্রৈমাসিক ডেট বুলেটিন এর তথ্য মোতাবেক, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে সরকারের মোট ঋণের (দেশি-বিদেশি) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯ লাখ ৪৪ হাজার ১৭১ কোটি টাকা।
মূলত ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ঋণের পরিমাণ অত্যধিক পরিমাণ বেড়েছে। ২০০৯ সালে সরকারের ঋণ ছিল মাত্র ২ লাখ ৭৬ হাজার ৮৩০ কোটি টাকা। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ‘মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক’ নীতিতে বলা হয়েছে যে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের শেষে সরকারের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৬ লাখ ৩ হাজার কোটি টাকা। সরকার ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়। ট্রেজারি বিল-বন্ডের মাধ্যমে সরকার ঋণ নেয়। এছাড়া সঞ্চয়পত্র, সঞ্চয় বন্ড, প্রাইজ বন্ডের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকেও সরকার ঋণ নেয়।
প্রতি বছর রাজস্ব আয় বাড়াতে সরকার ব্যর্থ হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে কর অব্যাহতির সংস্কার চালু রাখা হয়েছে। কর ফাঁকির পরিমাণ বেড়েই চলছে। কর জাল বিস্তৃত করা যাচ্ছে না। পরোক্ষ করের ওপর নির্ভর করে রাজস্ব আয় বাড়াতে হচ্ছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর তথ্য মোতাবেক, এ পর্যন্ত বাংলাদেশে কর ফাঁকির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ২৩০ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে কর্মরত অনিবন্ধিত ৬ লাখ বিদেশি কর ফাঁকি দিচ্ছেন ১৮ হাজার কোটি টাকার ওপর।
দুর্বল করকাঠামো, দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে সরকারকে দেশি-বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তবে বিগত কয়েক বছরে ঋণের ওপর নির্ভরতা অনেক বেড়ে গেছে। ২০২২ সালের শেষ থেকে ২০২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক আমানত বাড়ছে ৩ লাখ ৯ হাজার ৮৮৮ কোটি টাকা। অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, আড়াই বছরে বর্ধিত আমানতের ৮৭ শতাংশই ঋণ নিয়েছে সরকার। এমনকি ২০২৯ সালে সরকার অর্থসংকটে পড়ে বিশেষ উদ্দেশ্য ট্রেজারি বন্ড ছেড়েও ঋণ নেয়।
বর্তমান ইউনূস সরকারও ঋণ সহায়তা চাইছে। খারাপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ইউনূস সরকার উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা দিতে অনুরোধ করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডেও সক্ষমতা না থাকার কারণে ঋণ সহায়তা চাওয়া হচ্ছে। সব সরকারপ্রধান একই নীতি অবলম্বন করছে। বর্তমানে বৈদেশিক ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০ বিলিয়ন ডলার। এখন প্রশ্ন হলো, বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ এত বাড়ল কেন এবং সরকার কীভাবে ঋণ (আসল ও সুদ মিলে) পরিশোধ করবে।
সম্প্রতি শিক্ষা উপদেষ্টা বলেছেনে, সরকার এখন ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ করছে। ইআরডি তথ্য মোতাবেক, ২০২৪-২৫-এর প্রথম ১১ মাসে বৈদেশিক ঋণের ৬৮ শতাংশ ব্যয় হচ্ছে আগের নেওয়া ঋণ পরিশোধে। অর্থ উপদেষ্টা বলেছেন যে, ঋণ ব্যবস্থাপনায় কৌশলী হতে হবে। পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেছেন যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট হবে ঋণের দুষ্টচক্র ভাঙার। তিনি আরো বলেন যে, বাজেটে ঋণনির্ভরতা কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা করা হবে। বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় এটা কি সম্ভব? বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের বিষয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ৪১টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এবং বিশ্বব্যাংকের কাছে অতিরিক্ত ঋণসহায়তা চাওয়া হচ্ছে। দুঃখজনক যে, বৈদেশিক মুদ্রার মজুত এখন ঋণনির্ভর হয়ে পড়েছে। নানা কারণে কাঙ্ক্ষিত বিদেশি বিনিয়োগ আসছে না। বৈদেশিক ঋণে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বাড়লে আমরা গর্ব করছি। বৈদেশিক ঋণে রিজার্ভ বাড়লে, এটা টেকসই নয়। রিজার্ভ বাড়াতে হবে রপ্তানি আয় এবং প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স দিয়ে। তাহলে টেকসই হবে। উল্লেখ্য, বিগত সরকারের সময় বৈদেশিক ঋণ নিয়ে কিছু শ্বেতহস্তী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। এখন সেই প্রকল্পগুলো থেকে প্রত্যাশিত আয় আসছে না। যার কারণে ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে।
কর্ণফুলী টানেল, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, মাতারবাড়ী বিদ্যুত্ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুত্ প্রকল্প সমালোচিত হয়েছে। শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি বলেছে যে, ৭ মেগা প্রকল্পের শুরুতে যে ব্যয় ধরা হয়েছিল, চূড়ান্তভাবে তার চেয়ে ৮০ হাজার কোটি টাকা বেশি ব্যয় করা হয়েছে। অনেক প্রকল্প ব্যয় ৯০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বলেছে যে, বাংলাদেশে প্রকল্প ব্যয় বিশ্বেও সর্বোচ্চ। এর কারণ রাজনৈতিক। দ্বিপক্ষীয়ভাবে বেশি ঋণ নেওয়া হয়েছে। চীন এবং রাশিয়ার কাছ থেকে। দ্বিপক্ষীয় ঋণে তদারকি থাকে না। এ ধরনের ঋণে দুর্নীতি হয় রাজনৈতিকভাবে। বিগত সরকারপ্রধানের ঘনিষ্ঠ জন ৮২টি প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ছিল। এখন সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ হলো বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ।
এবারের বাজেটে ব্যয়ের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে সরকারের ঋণ পরিশোধ। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) তথ্য বলেছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ যে পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ নিয়েছে তার জন্য ২০২৯ সাল থেকে ২০৩২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে প্রতি বছর ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি আসল পরিশোধ করতে হবে।
বলা হচ্ছে যে, বিগত সরকারের সময় বেশির ভাগ বৈদেশিক ঋণ ‘অডিয়াস ডেট’ বা বিতর্কিত ঋণ। জনগনের স্বার্থের কথা বিবেচনা না করে যে ঋণ নেওয়া হয় তা-ই বিতর্কিত ঋণ বলে অভিহিত করা হয়। বিশ্বের অনেক দেশ বিতর্কিত ঋণ পরিশোধ করার বিষয়ে দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে ছাড় পেয়েছে। বিতর্কিত ঋণ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনেক দেশ আইনি কাঠামো তৈরি করেছে। ইকুয়েডর, কিউবা, ইরাক, মোজাম্বিক যারা অডিয়াস ডেটকে চ্যালেঞ্জ করে বিদেশি ঋণ মওকুফের সুযোগ গ্রহণ করেছে।
‘অডিয়াস ডেট’ নিয়ে বিতর্ক চলছে লেবানন, গ্রিস এবং শ্রীলঙ্কায়। আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক বলছে যে, মোট ঋণের পরিমাণ জিডিপির ৫৫ শতাংশ এবং বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ জিডিপির ৪০ শতাংশ পর্যন্ত থাকলে সেটি নিরাপদ। বলা প্রয়োজন, যে অর্থনীতিতে কর-জিডিপি অনুপাত থেকে ঋণ-জিডিপি অনুপাত বেশি হারে বাড়ে, সে অর্থনীতিতে আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ কতটা কার্যকর। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের বিপরীতে ঋণের হার বেড়েছিল ১৬ দশমিক ৫৩ শতাংশ। এটা সত্য যে, বাংলাদেশে রাজস্ব আয়ে দ্রুত পরিবর্তন আসবে না। অর্থাত্, রাজস্ব আয় এত সহজে বাড়বে না। সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সংস্কার করার জন্য বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণ বেড়েই চলেছে।
এমতাবস্থায় সরকারের করণীয় হবে, বিতর্কিত ঋণকে মওকুফের চেষ্টা করা, যা অন্য দেশ করেছে। সরকার ঋণ পুনর্গঠন করার জন্য দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারে। শ্রীলঙ্কা ইতিমধ্যে ঋণ পুনর্গঠন চুক্তি সম্পন্ন করেছে। ছাড়কৃত ঋণ অত্যন্ত সুচারুভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে প্রকল্প থেকে কাঙ্ক্ষিত রিটার্ন আসে। ঋণ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ব্যর্থ হলে ঋণের ফাঁদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এক বার ঋণের ফাঁদে পড়ে গেলে সারা বিশ্বের কাছে বাংলাশের অর্জিত সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঋণ ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত কৌশলী হতে হবে।
লেখক : অর্থনীতি বিশ্লেষক এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর সদস্য
(এই লেখার সম্পূর্ণ দায়ভার লেখকের একান্ত; এর সঙ্গে দৈনিক মূলধারার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই)