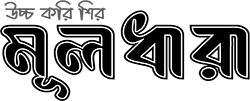প্রতি বছর বিশ্বে যে পরিমাণ ইলিশ ধরা পড়ে, তার ৭৫ ভাগই বাংলাদেশে; ২০ ভাগ ভারতে, ৫ ভাগ মায়ানমার ও অন্যান্য দেশে। তবে আর্ন্তজাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ফিস-এর মতে, বিশ্বের ৮৬ ভাগ ইলিশ বাংলাদেশে আহরিত হয়। বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী, মোহনা, উপকূল বঙ্গোপসাগরে এই ‘ইলিশা’ প্রজাতি ব্যপকভাবে পাওয়া যায়। ইলিশার সাথে মাঝে মধ্যে এর অন্য প্রজাতি চন্দনা এবং সার্ডিনও ধরা পড়ে। তবে ইলিশের জীবন চক্র অনুযায়ী এর অবন্থান ভিন্ন। মূলত ইলিশ সামুদ্রিক মাছ। বিজ্ঞানীদের মতে, স্বাদ ও জাত দুটোই হারিয়েছে আমাদের প্রাণের এ মাছটি।
সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে প্রজননের জন্য সাগর থেকে স্রোতের বিপরীতে মোহনা ও নদীতে প্রবেশ করে ইলিশ। এ সময় তার গতি ঘন্টায় একশ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। সাধারণত এক বছর বয়সেই ইলিশ পরিপক্ক হয়। তবে দুই বছর বয়সে একটি স্ত্রী সর্বোচ্চ ডিম ধারণ করে। বড় সাইজের একটি স্ত্রী ২০ লক্ষ পর্যন্ত ডিম ধারণ করতে পারে। নদী ও মেহানার স্বাদু ও অল্প লবণ পানিতে স্ত্রী ডিম ছাড়ার পর পুরুষ সাথে সাথে বীর্য ছড়িয়ে ডিম নিষিক্ত করে। ডিম ফুটে রেনু বের হয়। নদী ও মোহনায় পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার ডায়াটম, রটিফার, এলজি থাকে। রেনু পোনা এসব খাবার খেয়ে তরতর করে বেড়ে ওঠে। তিন মাস পরে এটি পরিণত হয় কিশোরে। নাম হয় তার জাটকা। জেলেরা তাকে কারেন্ট জালে আটকায়। জাটকা ও ডিম ওয়ালা ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ হলেও এগুলো হরহামেশাই হাটে-বাজারে বা নদী এলাকায় চোখ পড়ে। এদিকে জাটকা ও তার মা বাবা সবাই আবার সাগরে তাদের আদি নিবাসে বা লবণ পানির দিকে দৌড়ায়। কিশোর জাটকা সাগরে গিয়ে যৌবণ-প্রাপ্ত হয় এবং পরে পরিপক্কতা লাভ করে।
ডিম ছাড়ার সময় বা ডিম ছাড়ার পর পরই যেগুলো ধরা পড়ে, সেগুলোর স্বাদ বেশী হয়। পরিপক্ক ইলিশে প্রচুর ফ্যাট বা চর্বি থাকে। স্বাদ মুলত ফ্যাটের জন্য হয়। তবে সাধারণত রান্নার সময় মসল্যার কারলেও স্বাদের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। শুধু অর্থনীতি নয়, পুষ্টিগুণেও ইলিশ সেরা। ইলিশ প্রোটিন, স্নেহ, ভিটামিন এ, ডি এবং খনিজ উপাদান পটাসিয়াম, ক্যলসিয়াম, জিংক, আয়রন সমৃদ্ধ। ইলিশের স্নেহ-তে আছে ওমেগা-৩ পলিআনসেচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। ওমেগা-৩ পলি আনসেচুরেটেড ফ্যাটি এসিড হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও বাতজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভুমিকা পালন করে।
জীবন্ত ইলিশ আমরা পাই না। ইলিশ ধরার পর পানি থেকে উঠালেই আর বাঁচে না। অতিরিক্ত তেল বা চর্বিযুক্ত হওয়ায় আভ্যন্তরীণ অসমোরিগুলেশন বা অভিস্রবন চাপ বেড়ে গিয়ে তার সমস্ত রক্তনালী ফেটে যায় এবং প্রাণ হারায়। গবেষকরা বলছেন, পদ্মা-মেঘনায় ইলিশ ডিম ছাড়ার পর বিভিন্ন বাধার কারণে অনেক ইলিশই আর সাগরে যেতে পারে না। এভাবে ইলিশ এখন লোনা, আধা লোনা এবং স্বাদু পানি এই তিন জাতের ইলিশে আবির্ভূত হয়েছে।
অনেকের কথা, পদ্মায় ইলিশ থাকলে পুকুরে কেন নয়। পুকুরে মিঠা পানিতে ইলিশ চাষ নিয়ে চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে সফল হননি। ইদানিং গবেষকদের ধারণা, ইলিশের লবন সহিষনুর জিনোম সিকোয়েন্স-এর মোডিফাইড ঘটিয়ে স্বাদু পানির জীন বিন্যাসে পরিবর্তন করা গেলেই পুকুরের ইলিশের স্বপ্ন পূরণ সম্ভব। তাই আলাদাভাবে শুধু পদ্মার ইলিশের উপর গবেষণা করার জন্যও অনেকে মত প্রকাশ করেছেন।
মনে রাখতে হবে, আমরা মূলত ইলিশ উৎপাদন করি না। আহরণ করি। বলা যায়, ইলিশ জলীয় প্রাকৃতিক সম্পদ। বরং আমরা আইন না মেনে জলীয় পরিবেশের প্রাকৃতিক উৎপাদনকে বাধাগ্রস্ত করছি।
ইলিশ চেতনা এখন ঘরে বাইরে সীমান্ত পেরিয়ে। বাঙালীর অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিহঙ্গ হংস বলাকা। দেশের প্রায় ৬ লাখ মানুষ সরাসরি ইলিশ আহরণে এবং ২৫ লাখ মানুষ এর ব্যবসার সাথে জড়িত। জিডিপিতে ইলিশের অবদান ১.১৫ শতাংশ। ২০১৭ সালে জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচুয়েল প্রপারটি অরগানাইজেশন বাংলাদেশের ইলিশকে ভৌগোলিক নির্দেশক আ জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা ইলিশের প্রজননক্ষেত্র রক্ষা তথা উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কৌশলগত বিভিন্ন কর্মসুচী অব্যাহত রেখেছে।
কথিত আছে, ইলিশের জন্য খাবার দেওয়া লাগেনা , চুন-সার-ঔষধ দেওয়া লাগে না। তবু কেন ইলিশ সবাই কিনতে পারে না। কেন এত দাম?
মহাজনের দাদন নিয়ে লম্বা সময় ধরে সাগরে গিয়ে অনেক ট্রলারই মাছ না পেয়ে ফেরত আসে। মাঝে মাঝে খবর হয় সাগরে জেলেরা নিখোঁজ বা জলদস্যুরা মুক্তিপণ চেয়ে জেলেদের মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। আবার ঘাট থেকে আড়ত ও বাজারে আসতে সিন্ডিকেটের বিষয়টিতো আছেই!
গবেষকরা বলছেন, দেশের ৭২ ভাগ জীবনজীবিকা জল ও প্রকৃতি নির্ভর। ফলে প্রাকৃতিক আহরণ তার সহনশীলতার মাত্রাকে অতিক্রম করেছে। ফলে আগের মত প্রাকৃতিক উৎসের খাদ্য উপাদান মিলছে না। পানির প্রবাহ , ভূপ্রকৃতির গাঠনিক পরিবর্তন, জলবায়ুর পরিবর্তন আর মানুষের নেতিবাচক কর্মকান্ডের ফলে আমাদের জলজ সম্পদ ইলিশ অনেকটাই সংকটে। একটি পরিকল্পিত ডেল্টাপ্লান এবং তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতি ও অর্থনীতির এই শক্তিটি আরো শক্তিশালী হোক—এটাই প্রত্যাশা।
লেখক : মৎস্যবিদ। মোংলা, বাগেরহাট।
(এই লেখা লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত; এ সংক্রান্ত কোনো দায় দৈনিক মূলধারা বহন করবে না)